ক্যালিডোস্কোপে দেখি – ১৭
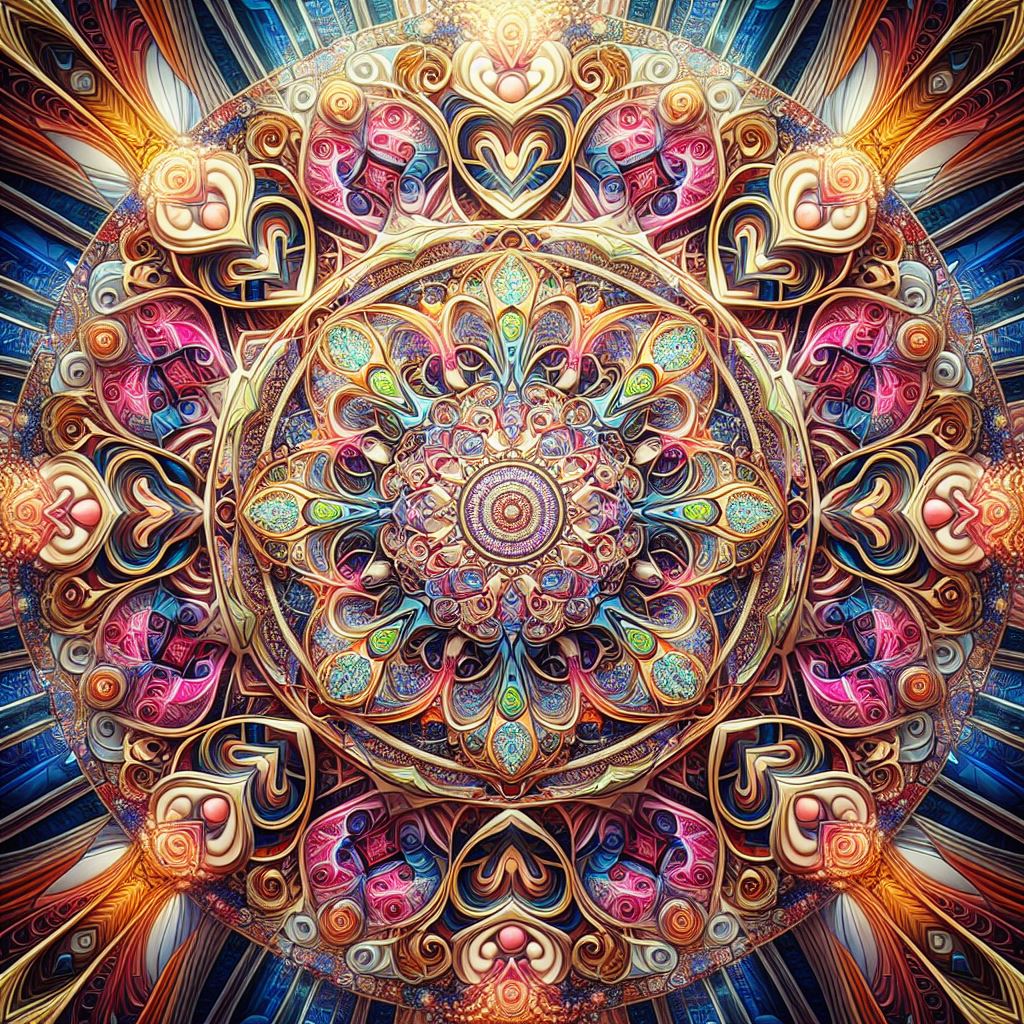
ক্যালিডোস্কোপ-১১ || মেয়েদের দিন, মায়েদের দিন *** *** নারী দিবস। মাতৃ দিবস। আমার মা-এর কাছে এই দিবসগুলি কোন বিশেষ বার্তা আনে না। তা বলে বার্তাগুলি থেকে তিনি দূরে থাকেন না। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন। খবরের সাথে নিজেকে সংপৃক্ত রাখেন। বস্তুতঃ সেই পাঠ-ই তাঁকে সচল রেখেছে। কিন্তু তাঁর চারপাশের দুনিয়ায় তিনি অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছেন। তাঁর মানসিক আর শারীরিক সক্ষমতার যতটা অবশিষ্ট আছে, তাতে উন্নত দেশের বাসিন্দা হলে তিনি এখন-ও সক্রিয় জীবনযাপন করতেন। কিন্তু নিজের দেশে, সন্তানের সংসারে শিশুপালনের ভূমিকা পার হয়ে গেলে নিজের জনেদের মধ্যে থেকেও অনেক কাল-ই তিনি তাঁদের চলমান, ঘটমান জীবন প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন। তাঁর মত, তাঁর বয়সীরা আরও অনেকই। সেখানে সেটাই রীতি। রীতির প্রভাব বড় ব্যাপক। রীতি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের জীবন যাপন। কিন্ত, রীতিরা চিরকাল একইরকমই ছিল কি? থাকে কি? তারা কি অলঙ্ঘ্য? ভাঙ্গা যায়না তাদের? উত্তরবঙ্গের দিনগুলিতে আমাদের জীবনে রেডিও ছিল না, টিভি ত তখন আমাদের কল্পনাতেও নেই। তা বলে, অবসরে গল্পের অভাব ছিল না। মা গল্প করত, ঠাকুমা গল্প করত। তাদের জীবনের গল্প। সে গল্পে অনেক সময় আমাদের চারপাশের জীবনের সাথে অপরিচিত রীতির গল্পও ফুটে উঠত। আমার সেই শৈশবের গল্পে কোন সুপারম্যান ছিলনা। ছিল এক সুপারওম্যান – আমার ঠাকুমার মা। তাঁর নানা ডাকাতেপনার কীর্তির গল্প শুনতাম। ভুলে গেছি এখন সে সব, দু’টি বাদে। এক, তিনি হুঁক্কা খেতেন। ধূম্রপান নিশ্চয়ই ভালো না। কিন্তু ধূম্রপান আমাদের সময়ে শুধু পুরুষরাই করত। সেই ট্যাবু তিনি মানতেন না। সম্ভবতঃ তাঁর পরিমণ্ডলে আরও কোন কোন মহিলা মানতেন না। লিখতে লিখতে ভাবছি, ঠিক লিখছি ত? না কি সবটাই আমার কল্পনার কারসাজি! দুই, এইটিতে মজা পেতাম খুব। ঠাকুমাদের বাড়িতে একটা লম্বা, কফিন ধরণের সিন্দুক ছিল। সেটির মধ্যে দামী বাসনকোসন থাকত, টাক-পয়সাও থাকত। ভারী সিন্দুক। রাতে ঠাকুমার মা, বেশ বয়স তখন তাঁর, সিন্দুকের উপর কিছু একটা পেতে সেই বিছানার নীচে একট শান দেওয়া দা (বা কাটারি) রেখে ঘুম যেতেন। একদিন এলাকার এক ওস্তাদ চোর সিন্দুকের উপর ঠাকুমার মায়ের পাশে এসে শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে তাঁকে ঠেলতে থাকে। গভীর ঘুমে নিমগ্ন ঠাকুমার মা কিছু টের পাননি। মাটিতে পড়ে গিয়েও নাক ডাকাতে থাকেন। চোর এরপর ঐ সিন্দুকের ঢাকনা খোলার চেষ্টা করে। ভারী ঢাকনা নিঃশব্দে তুলতে না পেরে একসময় অসাবধানে ঠাকুমার মাকে জাগিয়ে ফেলে। কি ঘটছে তা মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিয়ে সে মহিলা লাফিয়ে উঠে চোরকে জাপটে ধরে চিৎকার জুড়ে দেন। তবে, চোরও তৈরী হয়ে এসেছিল। তার তেল মাখা গা ঠাকুমার মায়ের কঠিন কব্জা থেকে পিছলে যায়। খানিকটা দূর পর্যন্ত ধাওয়া করে ঠাকুমার মা হাল ছেড়ে দেন। এত বছর পর এ গল্প মনে করতে গিয়ে খুঁটিনাটিতে ভুল হতে পারে। কিন্তু যেটায় আমি নিঃসন্দেহ – সাহসী, সক্রিয় জীবনযাপনের যে রীতির ছবি সে গল্পে ধরা পড়ত সেটা বেশ আকর্ষণীয় ছিল। ঢাকা-বিক্রমপুরের গ্রামাঞ্চলে সেই রীতির জীবন আজো প্রবাহিত হয় কি? আপনারা হয়ত বলতে পারবেন। এই মহিলা ছিলেন গল্পের চরিত্র। কিন্তু গল্প যিনি করতেন, তিনি নিজেও ছিলেন সাহসী দৃপ্তচেতা মহিলা। বাবার শৈশবেই তাকে এবং আরও ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে ঠাকুমা বালবিধবা হয়েছিলেন। পানাম-এর সম্ভ্রান্ত হিন্দু বিধবা কলকাতায় পড়তে যাওয়া ছেলের সন্ধানে একাই রেলের গাড়িতে চেপে কলকাতায় চলে আসেন। খুঁজে বার করেন ছেলেকে। বাড়ি বাড়ি কাজ করে ছেলের এবং নিজের বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করেছেন। তবে সেসবও ত গল্পে শোনা। চোখের সামনে দেখা কাজ-কর্মের ফলে আমার প্রথম সাধারণের উচ্চতার উপরে মাথা তুলে রাখা মানুষ, আমার মা। আমি যখন উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, তিনিও স্থানীয় মেয়েদের বিদ্যালয়ে উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন, আমার-ই মতন পঞ্চম শ্রেণীতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন বয়স্ক শিক্ষার এক বিশেষ কার্যক্রম চালু করেছিল, বছরে দুটি করে ক্লাস শেষ করার। মা তাঁর ক্লাসে প্রথম হয়ে বছর শেষে সপ্তমশ্রেণীতে উঠে গেলেন। অনেক স্বপ্ন ছিল তার। সেভাবে পূরণ হয়নি। বাবার উত্তরবঙ্গের কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে আমরা যেখানে চলে আসলাম সেখানে ঐ শিক্ষা-কার্যক্রম চালু ছিলনা। ফলে এর পর দু’-তিন বছর ধরে একাই বাড়িতে পড়াশোনা করে ‘প্রাইভেট’-এ পরীক্ষা দিয়ে ‘হায়ার সেকেন্ডারী’ উত্তীর্ণ হন। কলেজ-এও ভর্তি হয়েছিলেন। আমাদের পড়াশনা-খাওয়া-পড়ার দেখভাল করতে করতে সেই শিক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষায় আর তার বসা হয়নি। অভাবের করাল হাতছানিতে আমাদের তখন দিশেহারা অবস্থা। তবু আজ পিছন ফিরে মনে হয় আমার আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ানো উচিত ছিল। যে করেই হোক তাঁর ‘গ্রাজুয়েট’ হওয়ার স্বপ্নটার জন্য লড়ে যাওয়া দরকার ছিল। বিয়ের আগের দিনগুলোয় মার লেখা পড়া করা হয়ে ওঠেনি। মেয়েদের লেখাপড়া করানোর তেমন রীতি ছিল না। কিন্তু আমরা বড় হতে হতেই রীতি পাল্টে গিয়েছিল। এমন কি বিবাহিত, তিন ছেলের মা হওয়ে যাওয়া মেয়েও পড়ালেখার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিল। রীতি পাল্টে গিয়েছিল। তবে রীতিরা ত আর হঠাৎ করে পালটায় না। আমাদের উত্তরবঙ্গের দিনযাপনের সময়গুলোয় পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে ঝড়ের প্রস্তুতি চলছিল। বাবার সাথে প্রথম একদিন গেলাম এক জনসভায়। অজয় মুখোপাধ্যায় মূল আকর্ষণ। জ্যোতি বসু ছিলেন কিনা মনে নেই। বসুর থেকেও মুখোপাধ্যায়ের ক্যারিশ্মা তখন বেশী ছিল। বিপুল উত্তাল জনসভা। রাজনীতির সাথে সেই প্রথম পরিচয়। তারপর ত ঝড় এসেই গিয়েছিল। আর সেই ঝড়ে কত যে পুরানো রীতিনীতি ঝরে গেল। জীবন যাপন এক থাকে নি তারপর। এর পরে আমার উত্তরবঙ্গের জীবন শেষ হয়ে গেল। বাবা বদলি হয়ে চলে এল দক্ষিণ বঙ্গে। নদীয়া, ২৪ পরগণার জীবনযাত্রার স্রোতে এসে মিশল আমাদের জীবন। যতদিন তসলিমা নাসরিনের লেখা না পড়লাম ততদিন ঠিক কথাটার সন্ধান পাইনি। বাবার বদলির চাকরীর সুবাদে ক্রমাগত ঠিকানা বদলে যাওয়ায় আর আমার অন্তর্মুখী মনের সুবাদে আমার ‘ছেলেবেলা’ বলে স্মৃতিটা খুব মজবুত নয়। কিন্তু বড় হয়ে ওঠার পুরো কালটা জুড়ে নানা বয়সী অনেক মেয়ের জীবনের ছায়ায় কাটানোর ফলে লম্বা সময় জুড়ে নানান মেয়েবেলার কাহিনীর চরিত্র হয়ে গিয়েছি। সে কাহিনীগুলি আলাদাভাবে মনে পড়ে না। একটা সামগ্রিক প্রভাব রেখে গেছে আমার উপর। আমার প্রথম বিদগ্ধ বন্ধু ছিল আমার মা। ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতি সচেতন মার সাথে আমার নিয়মিত আড্ডা হত, আজো হয়। মা’র লেখাপড়ার সূত্র ধরে তার বন্ধুদের সাথেও মিশতাম বেশ সহজভাবেই। সেই দিদিদের সুবাদে মেয়েদের সাথে মেশায় আমার কোথাও কোন জটিলতা পাকিয়ে ওঠেনি কখনো। মেয়েজীবনের নানা হতাশা-আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ-বেদনার সাথে পরিচিত ছিলাম। মা’র একটা সেলাই মেশিন ছিল। টানাটানির দিনগুলোতে তার ছেলেদের জামাপ্যান্ট মা নিজেই সেলাই করত। আবার নিজের বা অন্যান্য মেয়েদের সায়া-ব্লাউজও সেলাই করত। আমি সেলাই-টা বুঝতাম, একটু আধটু হাত লাগাতাম। মেয়েদের পোশাক নিয়ে আমার সমবয়সী ছেলেদের মধ্যে যে উত্তেজনা কাজ করত আমার মধ্যে সেটা ছিল না। আমার মনে ঢেউ তুলত মেয়েদের কথা, কাজ। আমার যৌন চেতনায় প্রথম যে ধাক্কা দিয়েছিল সে আমার সমবয়সী এক মেয়ে। নাম ভুলে গেছি। ধরা যাক প্রতিমা। প্রতিমার মত সুন্দরী ছিল, ও নাম দিলে অবিচার হবে না। আমি তখন সম্ভবতঃ সপ্তম শ্রেণী। তিন-ভাই মিলে দল। জুটেছিল আরও কিছু ছেলে। আমার ছোট দুই ভাইই মহা ওস্তাদ। তাদের সাথে আমিও দাপিয়ে বেড়াই, দলে পড়ে। প্রতিমারও একটা ছোট মত দল ছিল, মেয়েদের। দুই দলে মাঝে মাঝে লড়াই বাধত খেলার মাঠের দখল নিয়ে। হাতাহাতি চলত। একসময় দেখলাম মারামারি আর হচ্ছে না, একটা বোঝাবুঝিতে পৌঁছে গেছে দুই দল। তার পর একসময় প্রতিমাদের দলটাকে আর দেখতে পাই না। ভাল, গোটা মাঠ আমাদের দখলে। কিন্তু প্রতিমার দেখা পাওয়া গেল, রাস্তায়, বাইসাইকেল ছোটাচ্ছে। আমারও তখন সাইকেল ছোটানোর ঋতু। সেই কারণেই দেখা পাওয়া গেল। এ মাথা-ও মাথা ছোটাছুটির পাল্লায় বেশীরভাগ সময়ই গন্তব্য হত বিপরীত মুখী। এইরকম-ই এক সাইকেল ছোটানোর দিনে দেখলাম প্রতিমা সাইকেল থেকে নেমে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। এক হাতে সাইকেলের হাতল ধরা। আর এক হাতে কাউকে ডাকছে। তীব্র রাগে ফেটে পড়ছে গলা, “এক লাত্থি মেরে যে দিক দিয়ে বেরিয়েছিস, সেই দিক দিয়ে মার পেটে ঢুকিয়ে দেব।” ভাষায় যৌনতা আমার চারপাশে নূতন কিছু ছিলনা। আমার কাছে যা নূতন ঠেকেছিল তা হল অত্যন্ত গোছান প্রস্তাবটি। আর সেটা একটা মেয়ের মুখ থেকে অমন সোচ্চারে প্রকাশ্য দিবালোকে ছিটকে আসা। উচ্চতায় খাটো হওয়ায় সারা শৈশব-কৈশোর আমি অনেক হেনস্তার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। বাড়ির রীতি মেনে গালি দিতে পারতামনা। ইচ্ছে করত খুব। ঐ প্রবল গালির কারণে প্রতিমা সেদিন আমার হিরো হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রথম সমবয়সী হিরো। সেই সাথে তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছিলাম এক সাহসী মেয়ের প্রতি। কিছুদিন বাদে প্রতিমার পায়ে বেড়ি পড়েছিল। বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার। তাকে রীতির সীমায় আটকে রাখা যাচ্ছিলনা। তার কিছুদিন বাদে শুনলাম প্রতিমা বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। বিয়ে ভাঙ্গাটা রীতি ছিলনা তখন। প্রতিমা রীতি ভেঙ্গেছিল। আমার সারাজীবন ধরেই দেখেছি রীতি ভাঙ্গা মেয়েদের। তারাই আমায় সাহস যুগিয়েছে সামনে এগোনোর। আমার এগোনোয় সমাজ সংসার কিছু ব্যাপকভাবে বদলে যায়নি। কিন্তু আমি ত একা নই। আরও কতজন এগোচ্ছে। এত এত মানুষের এগোনোয় বড় বদল ঘটবে না? আজ না হোক কাল? মাঝে মাঝে দু’-একটা কথা গুছিয়ে মন্তব্য লিখে ফেলতে পারলেও আমি প্রবন্ধকার নই। আর গুছিয়ে লিখতে গেলে উপকরণের সম্ভার লাগে। আমার তাও নেই। আমি বড়জোর স্মৃতিচারণ করতে পারি। যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা আমার বোধের কথা জানাতে পারি। সচলায়তনে নারীসপ্তাহ উপলক্ষে প্রকাশিত নানা লেখায় নারীর প্রতি যে বিপুল ব্যাপক অত্যাচারের চিত্র উঠে এসেছে, আমার যাপিত জীবনের মেয়েদের সামগ্রিক ছবি তার থেকে আলাদা নয়। কিন্তু আমি তুলে ধরতে চেয়েছিলাম কিছু আশার ছবি। আমার সহপাঠী মেয়েদের কাছ থেকে জেনেছিলাম জুতোর হিলের মাহাত্ম্য। পিছন থেকে অথবা পাশ থেকে ক্রমাগত ছোঁয়ার আক্রমণ চালানো দুর্বৃত্তের পায়ের উপর হিলের উপযুক্ত ব্যবহার কাজে এসেছে তাদের। কাজে এসেছে যূথবদ্ধতার শক্তিও। তবে এই সমগ্র ছবিটায় একটা বড় সীমাবদ্ধতা (ক্যাভিয়াট) আছে। সমস্ত অভিজ্ঞতাটাই ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বাংলায় হিন্দু মেয়েদের আমি যেমন দেখেছি, সেই ছবি। এদের রীতি ভাঙ্গার কাজে ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এমনকি আমার স্ত্রী যেদিন সিঁদুর রাখতে রাজী হয়নি, পদবী বিসর্জন না দিয়ে চালিয়ে গিয়েছিল যতদিন পারে, প্রণাম করতে অস্বীকার করেছিল তার ‘বর’-কে, দাবী করেছিল যে প্রণাম করতেই হলে সেটা করতে হবে উভয়ে উভয়কে, আর তার জীবনসঙ্গী করেছিল সেটা, কোন ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে তাকে থমকে যেতে হয়নি। তাকে শুধু রীতিগুলো ভাঙ্গতে হয়েছিল, তাকে এবং তার জীবনসঙ্গীকে। সকলের জন্য সেটা সহজ না হতেই পারে। দুনিয়ার নানা প্রান্তে চরম শাস্তির খড়গও নেমে আসতে পারে তাদের উপর। পারে, আজ। তারপর, কাল, পরশু? [প্রকাশিত – সচলায়তন, মে ১০, ২০১৫]
ক্যালিডোস্কোপ-১১ || মেয়েদের দিন, মায়েদের দিন *** *** নারী দিবস। মাতৃ দিবস। আমার মা-এর কাছে এই দিবসগুলি কোন বিশেষ বার্তা আনে না। তা বলে বার্তাগুলি থেকে তিনি দূরে থাকেন না। নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন। খবরের সাথে নিজেকে সংপৃক্ত রাখেন। বস্তুতঃ সেই পাঠ-ই তাঁকে সচল রেখেছে। কিন্তু তাঁর চারপাশের দুনিয়ায় তিনি অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছেন। তাঁর মানসিক…
Recent Posts
Categories
- Blog
- Book Chapter
- featured
- অঞ্জলি
- অনুবাদ
- অনূদিত কবিতা
- অনূদিত গল্প
- আলাস্কা গ্লেসিয়ার বে
- ঈশপের গল্প
- কবিতা
- কিছুমিছু
- ক্যালিডোস্কোপ
- ক্রুজ
- গল্পপাঠ
- গুরুচন্ডালি
- ছোট গল্প
- টুকিটাকি
- দুকূল
- নীতিকথার অনুবাদ
- পাঠ প্রতিক্রিয়া
- ফটোগ্রাফি
- বইয়ের হাট
- বাছাই
- বেড়ানোর গল্প
- মৌলিক কবিতা
- রুট ৬৬ গ্রুপ পোস্ট
- রুট ৬৬ শারদীয়া ২০২০
- সচলায়তন
- স্মৃতিকথা
